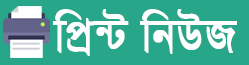কৃষিতে পরিবর্তন, কিন্তু কৃষকের জীবনে ভিন্ন

শ্যামনগর সাতক্ষীরা : কৃষকের সন্তান হিসেবে আমি বরাবরই উপলব্ধি করেছি আমাদের কৃষি ও কৃষকের সঙ্গে বাংলাদেশের নাড়ির সম্পর্ক। এই মাটি শুধু আমাদের খাদ্য যোগায় না, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির ভিত্তিও স্থাপন করে। অথচ, একটি গভীর বেদনা আমাকে তাড়িত করেÑআমাদের কৃষকরা, যারা অক্লান্ত পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলান, তারা প্রায়শই তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পান না। কৃষি, কৃষক এবং বাংলাদেশÑএই তিনটি শব্দ যেন একসূত্রে গাঁথা, একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু কৃষকের এই অপরিহার্য ভূমিকার প্রতিদান কি আমরা সঠিকভাবে দিই?
আজকের দিনে, কৃষকদের টিকে থাকার সংগ্রাম আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। জমিতে ফসল ফলানো এখন আর শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বিভিন্ন উপকরণের উপর নির্ভরশীল, যাদের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। পানি, সার, বীজ, শ্রমিকÑসবকিছুর দাম বেড়েছে, অথচ কৃষকের আয় বাড়েনি।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০% এখনো কৃষি খাতে যুক্ত। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭০% প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ে কৃষি খাতের অবদান এখনো ১২-১৪% এর মধ্যে অবস্থান করছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী, যারা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, তারা নিজেরাই টিকে থাকার লড়াইয়ে রয়েছেন।
কৃষিকাজ এখন আর সহজ নয়। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে কৃষকদের বিভিন্ন উপকরণ কিনতে হয়। এদের দাম বৃদ্ধি তাদের উৎপাদন খরচকে বৃদ্ধি করে তোলে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে সারের দামের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে সারের দাম কেজিতে ৫ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা কৃষকদের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল। বর্তমানে প্রতি কেজি ইউরিয়া সারের খুচরা মূল্য ২৭ টাকা। উদ্বেগের বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম কমলেও দেশের বাজারে তা এখনও বেশি। সরকার ভর্তুকি দিলেও, তা হয়তো কৃষকদের ক্রমবর্ধমান খরচ সম্পূর্ণরূপে লাঘব করতে পারছে না, এবং ভর্তুকি বিতরণেও নানা অনিয়ম দেখা যায়। মূলত, আমদানিকৃত সারের উপর নির্ভরতা কৃষকদের বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং মুদ্রার হারের পরিবর্তনের কাছে দুর্বল করে তোলে।
সেচের জন্য পানির খরচও কৃষকদের একটি বড় উদ্বেগের কারণ। ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণে সেচ ব্যয় বেড়েছে। সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ ব্যবস্থা একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প হলেও, এর ব্যাপক প্রচলন এখনও সীমিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় কৃত্রিম সেচের উপর নির্ভরতা আরও বাড়ছে, যা কৃষকের আর্থিক অবস্থাকে আরও দুর্বল করে তোলে।
বীজ একটি অপরিহার্য কৃষি উপকরণ, এবং এর দামও কৃষকদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বীজের দাম ২০-৩০% বৃদ্ধি কৃষকদের জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। প্রায়শই কৃষকদের সরকারি নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বীজ কিনতে হয়। সরকারিভাবে সরবরাহকৃত বীজের গুণমান এবং প্রাপ্যতা নিয়েও সমস্যা দেখা যায়, যার ফলে কৃষকরা আরও ব্যয়বহুল বিকল্প কিনতে বাধ্য হন।
অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের খরচ: এছাড়াও, কীটনাশক এবং শ্রমিকের মজুরিসহ অন্যান্য খরচও কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। কীটনাশকের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণের অভাব কৃষকদের জন্য একটি অতিরিক্ত বোঝা।কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের যে দাম পান, তার সাথে বাজারে ভোক্তাদের দেওয়া দামের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। এই ব্যবধানের ফলে কৃষকরা তাদের ন্যায্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত হন। ধানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কৃষকরা যে দামে ধান বিক্রি করেন, বাজারে চালের দাম তার থেকে অনেক বেশি থাকে। ধানের গড় উৎপাদন খরচ প্রায় ৩০-৩৫ টাকা/কেজি হলেও অনেক কৃষক ২৮-৩২ টাকায় বিক্রি করেন।
অথচ বাজারে চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে। পাটের বাজারেও কৃষকদের উৎপাদন খরচ প্রায়শই উঠে আসে না। পাট উৎপাদনে প্রতি বিঘায় ২৭ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হলেও, বাজারে ভালো মানের এক মণ পাট দুই হাজার ৮০০ থেকে তিন হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
সবজির ক্ষেত্রেও একই চিত্র, কৃষকরা অতি সামান্য দামে তাদের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হন, যেখানে ভোক্তারা অনেক বেশি দাম দিয়ে সেগুলো কেনেন। পেঁয়াজ ৩০-৩৫ টাকা খরচ করে উৎপাদন করেও বিক্রি করতে হয় ২০ টাকায়। বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৮০-১২০ টাকায়। টমেটো ৫ টাকায় বিক্রি করলেও শহরে তার দাম ৪০-৮০ টাকা। এমনকি, কৃষকদের শসা ও বেগুন পানির দামে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ার উদাহরণও রয়েছে।
কৃষক→ ফড়িয়া→ আড়তদার→ পাইকার→ খুচরা বিক্রেতা→ ভোক্তাএই চেইনে কৃষকের প্রাপ্ত মূল্য কমে আসে উল্লেখযোগ্য হারে। উদাহরণস্বরূপ: রাজশাহীতে পিয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৮ টাকা কেজিতে, কিন্তু ঢাকায় সেই পিয়াজের দাম ৩৫ টাকা! (সূত্র: প্রথম আলো, ফেব্রুয়ারি ২০২৪) মধ্যস্বত্বভোগীরা (ফোড়িয়া, ব্যাপারী, আড়ৎদার) এবং বাজার সিন্ডিকেটগুলো প্রায়শই কৃষকদের অসহায়তার সুযোগ নেয়। কৃষকদের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তারা কম দামে ফসল কিনতে বাধ্য করে এবং পরে সেই ফসল অনেক বেশি দামে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লাভ করে।
কৃষকদের সংগঠিত না থাকা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের পচনশীলতা এই মধ্যস্বত্বভোগীদের আরও শক্তিশালী করে তোলে। পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগার এবং কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে কৃষকরা তাদের পচনশীল ফসল দ্রুত বিক্রি করতে বাধ্য হন, প্রায়শই ন্যায্য দামের চেয়ে অনেক কম দামে। সুসংগঠিত বাজার এবং প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার অভাবও তাদের বিকল্প সীমিত করে তোলে। বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য প্রতি বছর নষ্ট হয় শুধুমাত্র দুর্বল সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণে। ন্যায্য দাম না পাওয়ার কারণে কৃষকদের জীবন ও জীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে।
অনেক কৃষক ঋণের জালে আবদ্ধ। তারা প্রায়শই উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে উৎপাদন খরচ মেটান এবং ফসল বিক্রি করে সেই ঋণ পরিশোধ করতেও হিমশিম খান। ক্রমাগত লোকসানের কারণে অনেক কৃষক তাদের জমি পর্যন্ত হারাতে বাধ্য হন। ন্যায্য দামের অভাব কৃষকদের মধ্যে হতাশা ও বিমুখতা সৃষ্টি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি খাতের জন্য ক্ষতিকর।
লাভজনকতার অভাবে গ্রামীণ যুবকদের কৃষিকাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা। কৃষকরা প্রায়শই সামাজিক স্বীকৃতি, দারিদ্র্য এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হন। কৃষি শ্রমিকদের মাঠে মৌলিক সুবিধার অভাব তাদের জীবনযাত্রাকে আরও কঠিন করে তোলে।
ভারত সরকার বছরে ২০টিরও বেশি ফসলে MSP (Minimum Support Price) ঘোষণা করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কৃষকদের জন্য কৃষি ভর্তুকি, জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি ও সরাসরি সহায়তা দেয়।
Minimum Support Price (ন্যূনতম সমর্থন মূল্য) বলতে বোঝায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সেই সর্বনিম্ন মূল্য যা কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য অবশ্যই পাবে। এর নিচে বাজারে ফসলের দাম নেমে গেলেও সরকার কৃষকদের কাছ থেকে সেই নির্ধারিত দামেই ফসল কিনে নেবে। ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের মূল উদ্দেশ্য হলো- কৃষকদের ফসলের দামের অপ্রত্যাশিত পতন থেকে রক্ষা করা, কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করা, কৃষকদের আয় স্থিতিশীল রাখা। জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (সরকার ন্যায্য দামে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কিনে খাদ্যশস্যের মজুদ গড়ে তোলে)।
বাংলাদেশে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (MSP): বাংলাদেশেও সরকার কিছু ফসলের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নির্ধারণ করে থাকে, বিশেষ করে ধান। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো: ধান কাটার পরপরই কৃষকদের মধ্যে ধান বিক্রির যে প্রবণতা তা থেকে রক্ষা করা, যখন বাজারে ধানের সরবরাহ বেশি থাকে এবং দাম কমে যায়। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা যাতে তারা ধান উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার এর জন্য ধান সংগ্রহ করা।
তবে, বাংলাদেশে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কিছু সমস্যাও রয়েছে। অনেক সময় মধ্যস্বত্বভোগীরা এর সুবিধা নিয়ে নেয় এবং প্রকৃত কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়াও, ক্রয় কেন্দ্রগুলোতে জটিলতা, দুর্নীতি এবং কৃষকদের অসচেতনতা ইত্যাদি কারণেও কৃষকরা সরাসরি এই ব্যবস্থার সুবিধা কম পায়। ভারতের মতো বাংলাদেশে ব্যাপক পরিসরে এবং বিভিন্ন ফসলের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য ব্যবস্থা চালু নেই। মূলত ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রেই সরকার বেশি মনোযোগ দেয়। সংক্ষেপে, ন্যূনতম সমর্থন মূল্য হলো কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা বাংলাদেশেও সীমিত আকারে প্রচলিত আছে।
কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়ার অভিযোগ করে থাকেন। ২০২৪ সালেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাজশাহীর কৃষক আব্দুল কুদ্দুসের ১০০ মণ টমেটো ৭ টাকা কেজি দরে বিক্রি করার ঘটনা এবং ফরিদপুরের মিজানুর রহমানের পেঁয়াজ ১৮ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ার চিত্র কৃষকদের অসহায় অবস্থার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ মাত্র। বাজারে সেই পেঁয়াজ ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে কৃষকের লাভ অধরাই থেকে গেছে।
এবছর শীতকালীন সবজি, বিশেষ করে বাঁধাকপির দাম অস্বাভাবিকভাবে কম ছিল। অনেক এলাকায় কৃষকরা পরিবহন খরচ পোষাতে না পেরে অথবা বাজারে ক্রেতা না থাকায় তাদের উৎপাদিত বাঁধাকপি ক্ষেতেই ফেলে রেখে নষ্ট করে দিয়েছেন। মাঠের পর মাঠ বাঁধাকপি পচে যাওয়ার দৃশ্য গণমাধ্যমেও উঠে এসেছে। কৃষকদের অভিযোগ, বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীরা সিন্ডিকেট করে দাম কমিয়ে রাখে, ফলে তারা ন্যায্য দাম পান না।
অন্যান্য শীতকালীন সবজির মতো আলুর দামও অনেক জায়গায় কৃষকদের উৎপাদন খরচের চেয়ে কম ছিল। হিমাগারে আলু সংরক্ষণের খরচ এবং বাজারে চাহিদা কম থাকায় অনেক কৃষক লোকসানের মুখে পড়েছেন। যদিও সরকার ধানের ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নির্ধারণ করে, অনেক কৃষক অভিযোগ করেন যে ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে তারা সেই দাম পান না। সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রির প্রক্রিয়াও অনেক সময় জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় প্রান্তিক কৃষকরা বাধ্য হয়ে কম দামে স্থানীয় বাজারে ধান বিক্রি করে দেন।
এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বাংলাদেশের কৃষকরা প্রতিনিয়ত নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া তাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এর ফলে অনেক কৃষক কৃষি কাজে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হতে পারে।
কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কৃষকদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে হলে কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন:
বাজার ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানো এবং কৃষকদের সরাসরি বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ তৈরি করা। ফসলের ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ক্রয় প্রক্রিয়াকে সহজ করা। পর্যাপ্ত সংখ্যক হিমাগার স্থাপন করা যাতে কৃষকরা তাদের ফসল সংরক্ষণ করে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারেন। কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা। বাজারদর এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কৃষকদের নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা। প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা।
যদি দ্রুত এসব পদক্ষেপ নেওয়া না হয়, তাহলে বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্র আরও ঝুঁকির মুখে পড়বে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে।
সরকার কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সার, বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। কিছু কৃষিপণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি নীতি প্রণয়ন এবং “স্মার্ট বাংলাদেশ” এর মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের কৃষি উপকরণে প্রবেশাধিকারের জন্য কৃষক কার্ড চালু করা হয়েছে। তবে, পুরনো চাষ পদ্ধতি, জমির খন্ড-বিখন্ডতা এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতার মতো চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে। ভর্তুকি বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ভর্তুকির সুফল প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। ন্যূনতম দাম নির্ধারণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।
কৃষক এবং ভোক্তাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, যেমন কৃষক বাজার, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং সমবায়। বিস্তৃত ফসলের জন্য ন্যায্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা। সরকারি উদ্যোগে ফসল ক্রয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভর্তুকি বিতরণে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। প্রান্তিক কৃষকদের কাছে সরাসরি নগদ অর্থ বা ডিজিটাল ভাউচার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা। দুর্নীতি রোধে কঠোর নজরদারি ও শাস্তির ব্যবস্থা করা। গ্রামীণ অবকাঠামো, বিশেষ করে সংরক্ষণাগার এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিতে বিনিয়োগ করা।
কৃষক সমবায় ও উৎপাদক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা, যাতে তারা দর কষাকষি করতে এবং বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে। বাজার সিন্ডিকেট দ্বারা কারসাজি রোধে এবং কৃষি মূল্য শৃঙ্খলে ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন নিশ্চিত করতে প্রবিধান ও তদারকি বাস্তবায়ন করা। কৃষকদের ফসল উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে এবং প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিংয়ের মতো মূল্য সংযোজন কার্যক্রমের জন্য সহায়তা প্রদান করা। কৃষকদের রিয়েল-টাইম বাজার তথ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা।
বাংলাদেশের কৃষকদের ন্যায্য দাম পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। তারা শুধু আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেন না, বরং আমাদের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিরও মূল ভিত্তি। তাদের অবদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা এবং তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আসুন, আমরা সকলে মিলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করি যেখানে আমাদের অন্নদাতারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সঠিক মূল্য পান এবং একটি সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারেন।
ভবিষ্যতের বাংলাদেশ যেন হয় এমন একটি দেশ, যেখানে কৃষকরা কখনো অভুক্ত থাকেন না।
© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত